লজ্জাবতী (Mimosa pudica) লাজুক উদ্ভিদের রহস্য ও উপকারিতা
আমি যখন প্রথম লজ্জাবতী গাছ দেখি, তখন সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ছোটবেলায় গ্রামের পথে হাঁটতে গিয়ে এই আগাছাসদৃশ গাছের পাতায় হাত দিতেই দেখি, মনের মতন লজ্জায় পাতা গুটিয়ে ফেললো! সে এক নিখাদ বিস্ময়ের মুহূর্ত – একটি গাছের যেন অনুভূতি আছে, স্পর্শ বুঝতে পারে। তখন থেকেই লজ্জাবতী গাছ আমার কৌতূহলের উৎস হয়ে থাকে। প্রকৃতির এত চমক যে একটা ছোট্ট উদ্ভিদও মানুষের মতো লাজুক আচরণ করতে পারে, সেটা ভেবে বেশ আবেগাপ্লুত হতাম। দিনে রোদ পড়লে আবার পাতাগুলি স্বাভাবিক হয়ে যেত, যেন কিছুই হয়নি। এভাবেই লজ্জাবতী আমার শৈশবের দুরন্ত কাণ্ডের সাথী ছিল।
লজ্জাবতী গাছ দেখতে সাধারণত ছোট একটি ঝোপালো লতা, কিন্তু এর গোলাপি-বেগুনি রঙের তুলতুলে গোল ফুলগুলো বেশ নজরকাড়া। পাতাগুলি খুব সূক্ষ্ম ছোট ছোট পত্রক দিয়ে বানানো পাখনার মতো – স্পর্শ করলেই মুহূর্তে তারা ভাঁজ হয়ে যায় এবং কয়েক মিনিট পরেই আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসেthedailycampus.com। গাছটির এই লাজুক ভঙ্গির কারণেই বাংলায় নাম হয়েছে “লজ্জাবতী”, অর্থাৎ লাজুক লতাteachers.gov.bd। গ্রামের বৃদ্ধদের কাছে শুনেছি, একসময় মাঠেঘাটে যত্রতত্র লজ্জাবতী দেখা যেত, কিন্তু এখন আগের মতো ততটা দেখা যায় না। তবু আজও যখন কোনো লজ্জাবতী গাছের সামনে দাঁড়াই, আমার ভেতরে সেই শিশুসুলভ বিস্ময় জাগে – আলতো স্পর্শে পাতা গুটিয়ে নিয়ে যেন বলে “লজ্জা পাচ্ছি”। এই গাছ শুধু মজার খেলা বা বিস্ময় নয়, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে বৈজ্ঞানিক রহস্য আর মানুষের জন্য উপকারী অনেক গুণ। আসুন, আমার প্রিয় এই লাজুক উদ্ভিদটির রহস্য ও উপকারিতা একসাথে näher জানার চেষ্টা করি। (নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি আপনাদের একজন কৌতূহলী বন্ধুর মতো)
লজ্জাবতী গাছের বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসা ও শারীরবৃত্তীয় তথ্যসহ কথোপকথনধর্মী বিশ্লেষণ
লজ্জাবতী: লাজুক উদ্ভিদের বিজ্ঞান ও গল্প
লজ্জাবতী গাছটিকে আমরা ছোটবেলা থেকেই চিনি সেই "লাজুক লতা" নামে – ছুঁয়ে দিলেই পাতাগুলো লজ্জায় সঙ্কোচন করে ফেলে!এটা সত্যিই একটা আশ্চর্য উদ্ভিদ, আর এর পিছনের বিজ্ঞানটা জানতে গিয়ে আমি নিজেই অবাক হয়েছি। আসুন, প্রথম-ব্যক্তির চোখে কথোপকথনের সুরে লজ্জাবতী গাছের পুরো গল্পটাই জেনে নেই। আমরা দেখবো এর বৈজ্ঞানিক পরিচয়, গঠন, বিস্ময়কর পাতার আচরণ, ঔষধি ব্যবহার, এবং এমনকি কীভাবে একে বীজ থেকে চারা করা যায়। (নিজে জানুন, অন্যকে জানান – ঠিক আমাদের ব্লগের মটো যেমন বলে!)
বৈজ্ঞানিক নাম ও শ্রেণীবিন্যাস
লজ্জাবতীর বৈজ্ঞানিক নাম Mimosa pudica। এটি ফ্যাবাসি (Fabaceae) পরিবারে, অর্থাৎ মটরশুটি-জাতীয় উদ্ভিদগুলোর আত্মীয়bn.wikipedia.org। উপপরিবার Mimosoideae-এর সদস্য এই গণের ("Mimosa") অধীনে প্রায় ৪০০ প্রজাতির গুল্ম ও লতা রয়েছে। আমাদের লজ্জাবতী সেই Mimosa গণেরই সবচেয়ে পরিচিত প্রজাতি। Mimosa pudica নামের pudica অংশের অর্থই লজ্জাশীলা বা লাজুক – মজা লাগে যে নামটা উদ্ভিদের স্বভাবের সাথেই মিলে যায়! এই গাছের ইংরেজি নামগুলোও মজার, যেমন Sensitive Plant, Touch-me-not ইত্যাদি। গ্রিক শব্দ "(mimos)" থেকে "Mimosa" নামটি এসেছে, যার মানে "অনুকরণকারী" – ইঙ্গিত করছে এই উদ্ভিদের পাতার সংবেদনশীল আচরণকে, যেন সচেতন প্রাণীর মতো অনুকরণ করে প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে।
শ্রেণীবিন্যাস: লজ্জাবতী উদ্ভিদ জগতের সপুষ্পক উদ্ভিদের অন্তর্গত। এর পরিবার Fabaceae (পুরনো নাম Mimosaceae), উপপরিবার Mimosoideae, এবং গণ Mimosa। বৈজ্ঞানিক নামের শেষে L. দেখা যায়, যা উদ্ভিদ বিজ্ঞানী লিনিয়াসকে (Linnaeus) সূচী করে। সাধারণ বাংলা নামে একে লজ্জাবতী, লাজুক লতা বা লজ্জালুও বলা হয়barta24.com।
গাছের চরিত্র ও পাতার গঠন
লজ্জাবতী একটি ছোট আকৃতির কাঁটাযুক্ত গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। উচ্চতায় সাধারণত মাত্র ০.৫ থেকে ১.৫ মিটার, অর্থাৎ দেড় থেকে পাঁচ ফুটের মতো লম্বা হয় jagonews24.com। এর কাণ্ড লতানো প্রকৃতির এবং কান্ডে ছোট ছোট কাঁটা থাকে – গাছটা দেখতেও একটু লাজুক কিন্তু রক্ষात्मक! পাতাগুলো যৌগিক পত্র, অর্থাৎ প্রতিটি পাতা আবার অনেকগুলো ছোট পাতিকা (leaflet) নিয়ে গঠিত। একেকটা পাতা অনেকটা শিমুলের পাতার মতো বা তেতুল পাতার মতো পালক-আকৃতির, সূক্ষ্মভাবে বিভক্ত ছোট ছোট পত্রক দিয়ে সাজানো থাকে। পাতার বোঁটা (petiole) থেকে চারটি পত্রদণ্ড বের হয় এবং প্রতিটি পত্রদণ্ডে বহু পাতিকা থাকে – বলুন তো, কী অপূর্ব বিন্যাস! পাতাগুলি দ্বিপক্ষল (bipinnate) ধরনের, যা স্পর্শকাতর উদ্ভিদের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পাতার রঙ উজ্জ্বল সবুজ, আর পাতিকা গুলো একটু লম্বাটে-কমলা ধরনের, ধারণা করুন যেন পাতাগুলো সারিবদ্ধ লম্বা পালকের মতো।
থোঁতা ও কাঁটা: লজ্জাবতীর কাণ্ডে ছোট ছোট কাঁটা থাকে যা গাছের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। এসব কাঁটা আসলে উদ্ভিদের ত্বকের বিশেষ কোষের অনুন্নত রূপ – সহজ ভাষায়, কিছু কোষ সম্পূর্ণ পাতা বা শাখা হিসেবে গড়ে না উঠে শক্ত-কঠিন কাঁটা হিসেবে রূপান্তরিত হয়। ফলে গরু-ছাগল অত সহজে এটি চিবিয়ে খেতে চায় না। আমি যখন এই কাঁটা দেখেছি প্রথমবার, ভাবছিলাম গাছটা বুঝি নিজেকেই বাঁচাতে গোপনে অস্ত্র বানায়! (মানুষের মতো কৌশলী না হলেও, উদ্ভিদের নিজের নিরাপত্তা বোধ কিন্তু দারুণ)।
ফুল ও বীজের পরিচিতি
লজ্জাবতীর ফুল ছোট, গোলাকার ফুলগুচ্ছ আকারে থোকায় ফোটে। প্রথমবার দেখলে ফুলকে একটু গোলাপি রঙের তুলতুলে বলের মতো লাগে – একদম অদ্ভুত সুন্দর! ফুলের রঙ সাধারণত গোলাপি-বেগুনি বা ফিকে বেগুনি হয়, কখনও সাদা রঙের ফুলও ফোটে। একটা মজার ব্যাপার হলো, অনেক সময় কথিত “পুরুষ” লজ্জাবতী গাছে গোলাপি-বেগুনি ফুল দেখা যায় আর “মেয়ে” গাছে ফোটে সাদা ফুল। যদিও উদ্ভিদজগতের দৃষ্টিকোণ থেকে লজ্জাবতীর পুরুষ-নারী আলাদা উদ্ভিদ নয় (এটি উভলিঙ্গ ফুল ধারণ করে), তবু এই ভিন্ন রঙের ফুলের কারণে এমন বলে থাকেন অনেকে। আমি নিজে গোলাপি আর সাদা দু’রকমের ফুলই গ্রামে দেখেছি, তখন আমিও ভেবেছি বুঝি আলাদা গাছ! ফুল থেকে ফল বা বীজতলি ধরে; ফলগুলো চ্যাপ্টা ও একটু বাঁকা ধরনের লম্বাটে শুঁটি, যার ভেতরে বীজ থাকে। বীজ আকারে ছোট, শক্ত এবং কালো রঙের হয়। একটি গাছে বেশ প্রচুর বীজ ধরতে পারে যদি সেটা পূর্ণবয়স্ক হয়।
লজ্জাবতী গাছের গোলাপি রঙের তুলতুলে ফুল (Sensitive plant এর ফুল)। প্রতিটা ফুল দেখতে ক্ষুদ্র মায়াবী বলের মতো, কী চমৎকার না!
জীবনচক্র ও প্রজাতি বিস্তার
লজ্জাবতী বর্ষজীবী (annual) আগাছা ধরনের উদ্ভিদ হলেও, অনুকূল পরিবেশে এটি বহুবর্ষজীবী গুল্ম হিসেবেও টিকে থাকতে পারে। সাধারণত বর্ষাকালে প্রচুর জন্মাতে দেখা যায়, তবে উষ্ণ আবহাওয়ায় সারা বছরই বেড়ে উঠতে সক্ষম যদি পানি-ধোঁপের ভালো জোগান পায় steemit.com। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে বছরে দুই-তিনবারও ফুল-ফল দেয়। ফল পেকে শুকিয়ে গেলে বীজ মাটিতে পড়ে যায় এবং সামান্য আর্দ্রতা পেলেই অঙ্কুরোদ্গম হয়। আমি নিজে দেখেছি, একবার যেই জায়গায় লজ্জাবতী জন্মায়, পরের বছরে আশেপাশে আরও দশটা গাছ গজায় – বীজ ছড়িয়ে দ্রুত উপনিবেশ গড়ার এতে বিপুল ক্ষমতা।
ভৌগোলিক বিস্তার: লজ্জাবতীর আদি নিবাস মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষ করে মেক্সিকো অঞ্চলকে উদ্ভিদের জন্মস্থান বলা হয়। তবে এখন এটা সত্যিকার অর্থেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে – বাংলাদেশ-ভারতসহ পুরো দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া, এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উষ্ণ অঞ্চলেও এই উদ্ভিদ দেখা যায়jagonews24.com। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে পুকুরপাড়, মেঠোপথের ধার, পরিত্যক্ত জমি সর্বত্রই লজ্জাবতীর দেখা মেলে। এটি এত ছড়িয়ে পড়েছে যে অনেক জায়গায় এটি আগ্রাসী আগাছা (invasive weed) হিসেবেও বিবেচিত হয়। তবে আমাদের চোখে এটি নিছক আগাছা নয়, এক দারুণ ভেষজ গুণসমৃদ্ধ উদ্ভিদ হিসেবেও পরিচিত।
প্রজাতির বৈচিত্র্য: যেমন আগেই বলেছি, লজ্জাবতী গণে প্রায় ৪০০ প্রজাতি আছে ! বেশিরভাগই আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলের স্থানীয় উদ্ভিদ। আমাদের পরিচিত লজ্জাবতী (Mimosa pudica) ছাড়াও এর কিছু কাছের আত্মীয় আছে। উদাহরণ হিসেবে তেইরা কাঁটা (Mimosa diplotricha) নামে একটি বড় আকারের কাঁটাওয়ালা প্রজাতি রয়েছেbn.wikipedia.org, যেটি আমাদের লজ্জাবতীর চাইতে আকারে বড় বলে কেউ কেউ একে "বড় লজ্জাবতী"ও বলেন। এছাড়া Mimosa rubicaulis, Mimosa pigra প্রভৃতি নামে কয়েকটি প্রজাতি ভারত উপমহাদেশে পাওয়া যায়। তবে মজার ব্যাপার, এদের সবারই পাতায় স্পর্শকাতরতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে – হয়তো ডিগ্রীতে কিছু পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু লজ্জাবতীর মতই স্পর্শে নুয়ে পড়ে। ভাবুন একবার, একটা গোটা গণের (genus) নামই রাখা হয়েছে লজ্জাবতীর নামে, কারণ এই বৈশিষ্ট্যটাই তাদের আইডেন্টিটি!
লজ্জাবতীর আশ্চর্য প্রতিক্রিয়া: পাতার সিসমোন্যাস্টিক চলন
আমরা সবাই জানি লজ্জাবতীর সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল স্পর্শ করলে এর পাতা লজ্জায় (বা ভয়ে?) বন্ধ হয়ে যায়। একে বৈজ্ঞানিক ভাষায় Seismonastic movement বা থিগমোন্যাস্টি বলে – যেটা আসলে উদ্ভিদের স্পর্শ-উদ্দীপনায় সৃষ্ট নড়াচড়া। প্রথম বার যবে আমি এই গাছ স্পর্শ করি, মনে হয়েছিল গাছটির বুঝি অনুভূতি আছে, ও লজ্জা পেয়ে সঙ্কোচন করছে! সত্যিটা অবশ্য একটু ভিন্ন এবং দারুণ বৈজ্ঞানিক।স্পর্শ করলে ঠিক কী হয়? লজ্জাবতীর পাতার বুনোটে বিশেষ সংবেদনশীল কোষ থাকে, যেগুলোর মধ্যে টার্গর (turgor) নামক তরল পদার্থ থাকেjagonews24.com। টার্গর বলতে উদ্ভিদকোষের ভেতরে জলচাপ বোঝায়, যা কোষকে ফুলিয়ে শক্ত রাখে – একে কোষের “পেশী শক্তি”ও বলতে পারেন। আমরা যখন আঙুল দিয়ে পাতাকে ছুঁই বা হালকা আঘাত করি, তখন সেই স্পর্শ-উত্তেজনা পাতার গোড়ায় অবস্থিত বিশেষ কলাকোষ (যাকে Pulvinus বলে) থেকে একধরনের বিদ্যুৎ-সঙ্কেত সারা পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বাস করুন আর না করুন, উদ্ভিদেও বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘটতে পারে – যদিও সেটা খুব ক্ষীণ মাত্রায়। এই বৈদ্যুতিক সংকেতের প্রভাবে পুলভিনাস অংশের কোষগুলো মুহূর্তের মধ্যে তাদের টার্গর চাপ হারাতে শুরু করে। কোষের ভেতরে থাকা পটাশিয়াম আয়ন দ্রুত এক পাশে সরে যায় এবং পানি কোষ ছেড়ে বাইরের আন্তঃকোষীয় ফাঁকে বেরিয়ে আসে।
ফলাফল? পাতার ঐ অংশের কোষগুলো হঠাৎ চুপসে যায়, অভ্যন্তরীণ চাপ কমে যায় এবং শক্ত হয়ে থাকা পাতিকা-সংযুক্ত টিস্যু ঢিলে হয়ে পড়ে। পাতাগুলো তখন নিজের ওজনেই ভেঙে (ভাঁজ হয়ে) নুয়ে পড়ে যায়। পুরো প্রক্রিয়াটা ঘটে সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে – আপনি চোখের পলক ফেলার আগেই পাতা জড়োসড়ো! এটা যেন উদ্ভিদের নিজস্ব ডিফেন্স মেকানিজম – হঠাৎ পাতা মুড়ে গাছটা নিজেকে ছোট করে ফেলে শিকারীর চোখে কম দৃশ্যমান হওয়ার প্রচেষ্টা, অথবা পাতার আকস্মিক নড়াচড়ায় শিকারী প্রাণী ভড়কে যেতে পারে। প্রকৃতির কী চমৎকার কৌশল, তাই না? একে উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা মনে করেন প্রতিরক্ষামূলক অভিযোজন, যা বছরের পর বছর ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে।
স্পর্শের আগে লজ্জাবতী পাতাগুলো সম্পূর্ণ প্রসারিত অবস্থায় স্বাভাবিক দেখতে লাগে (Putrajaya, Malaysia তে তোলা ছবিতে উদাহরণ)। এই অবস্থায় গাছটি শান্ত ও নির্ভার আছে।স্পর্শের তৎক্ষণাৎ পরে লজ্জাবতীর পাতাগুলো ভেঙে নুয়ে গেছে, ঠিক যেন লাজুক ভঙ্গিতে নিজেকে গুটিয়ে নিলো। কয়েক মিনিট পর আবার পাতা আগের অবস্থায় ফিরবে। আশ্চর্যজনক এই প্রতিক্রিয়াটি সিসমোন্যাস্টিক চলনের উদাহরণ।
স্পর্শ ছাড়াও আরও কিছু উদ্দীপনায় লজ্জাবতী পাতা বন্ধ হয়। যেমন, প্রচণ্ড তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বা সন্ধ্যা হলে (আলো কমে গেলে) পাতাগুলো ধীরে ধীরে বন্ধ হতে থাকে।সন্ধ্যার সময় যে নড়াচড়া, সেটি কিন্তু স্পর্শের কারণে নয় – তাকে বলে নাইকটিন্যাস্টিক চলন, আলো-অন্ধকারের পরিবর্তনে উদ্ভিদের দোলন। রাতের জন্য পাতাগুলো বন্ধ অবস্থায় “ঘুমিয়ে পড়ে” আবার সকালে সূর্য উঠলে খুলে যায়। সত্যি বলতে কী, লজ্জাবতীর নড়াচড়ার সবটাই কিন্তু লজ্জা পাওয়া বা সত্তা থাকার কারণে নয়, এসবই উদ্ভিদের ফিজিওলজিক্যাল প্রতিক্রিয়া (যদিও কাব্যিকভাবে ভাবতে আমাদের ভালোই লাগে যে গাছটি লজ্জা পাচ্ছে)।
পাতার সংবেদনশীলতা নিয়ে ছোট্ট পরীক্ষা
আমি একদিন ভাবলাম, লজ্জাবতীর পাতা কতটা সংবেদনশীল আর কত দ্রুত নড়ে সেটা মেপে দেখবো! ভাবনাটা একটু পাগলামী শোনাতে পারে, কিন্তু কীভাবে পরীক্ষা করি বলুন? সহজ একটা আইডিয়া হল, পাতা স্পর্শের পর কত সেকেন্ডে পাতা পুরোপুরি বন্ধ হয় তা স্টপওয়াচ দিয়ে মাপা। আমি সত্যিই এটা করেছি – হালকা একটা তুলো দিয়ে পাতিকে ছুঁয়েই ঘড়ি ধরলাম। দেখলাম, প্রায় ২ সেকেন্ডেরও কম সময়ে একটি পাতা সম্পূর্ণ ভাঁজ হয়ে গেল! এরপর অপেক্ষা করে দেখলাম ফিরে খুলতে কতক্ষণ লাগে: প্রায় ৫-১০ মিনিট পর পাতা ধীরে ধীরে আগের অবস্থায় ফিরে এলো। এই সময়টা অবশ্য পরিবেশের তাপমাত্রা, আগের উদ্দীপনার মাত্রা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে। বাড়িতে আপনারাও এটা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন – মজা লাগবে। এছাড়াও, উদ্ভিদ কী পরিমাণ স্পর্শে সাড়া দেয় সেটাও মাপা যায়। বিজ্ঞানীরা ইলেকট্রোড লাগিয়ে অ্যাকশন পটেনশিয়াল (বিদ্যুৎ সংকেত) পরিমাপ করেছেন লজ্জাবতীতেdocs.backyardbrains.com। আবার কেউ কেউ বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করে দেখেছেন, উদাহরণস্বরূপ কেবল একটা পাতিকাকে ছোঁয়ালে বনাম গোটা শাখায় ঝাঁকুনি দিলে সাড়া দেওয়ার তারতম্য হয় কি না। দেখা গেছে, হালকা স্পর্শে শুধু কাছের পাতাগুলো বন্ধ হয়, আর জোরে ঝাঁকুনি দিলে গোটা শাখাটাই নুয়ে পড়ে। আমার নিজের অভিজ্ঞতায়ও, আলতো ছোঁয়ায় একটি পাতিকা (leaflet) ভাঁজ হলেও জোরে টোকা দিলে আস্ত পাতা বা শাখা পর্যন্ত নুইয়ে যায়। এসবই সেই বৈদ্যুতিক সংকেতের প্রভাব-ব্যাপ্তির ফারাক। কি চমৎকার না, একটা গাছের সিস্টেম যেন নার্ভাস সিস্টেমের মত কাজ করছে? (ট্যাঞ্জেন্টে একটু বলে রাখি, এমন পর্যবেক্ষণ থেকেই কেউ কেউ ভুল করে ভাবেন গাছের অনুভূতি আছে প্রাণীর মতো, কিন্তু আসলে এই সাড়া দেয়াটা সম্পূর্ণ রাসায়নিক-ভৌত প্রক্রিয়া, অনুভূতি বা স্নায়ু নয়)।
আরেকটা মজার পরীক্ষা আমি পড়েছিলাম: বারবার স্পর্শ করার পরে লজ্জাবতী ধীরে ধীরে পাতার সাড়া দেওয়া কমিয়ে দেয়, অর্থাৎ অভ্যস্ত হয়ে যায়। একে habituation (অভ্যাসগত অনুকরণ) বলে। বারবার পাতাকে না ক্ষতি করেই ঝাঁকাতে থাকলে দেখা যায় পরে আর পাতাগুলো বন্ধ হচ্ছে না বা অনেক দেরিতে হচ্ছে। এর মানে গাছটি শিখে ফেলছে যে এই বারবার নাড়া তার জন্য বিপদ নয়, তাই শক্তি বাঁচাতে প্রতিবার রেসপন্স করছে না। কি জীবন্ত আচরণ মনে হয়, তাই না? অবশ্যই, এটা একটা গবেষণার বিষয়, সাধারণ বাসায় করলে হয়ত খুব স্পষ্ট নাও হতে পারে। তবে যারা বিজ্ঞানী, তারা চার্ট বানিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে কয়েকবার পর স্পর্শে পাতার কোণ আগের মতো ভাঁজ হয় না – বলা যায় গাছটি “বোর” হয়ে যায়! (আমি কিন্তু এতে গাছকে জড় ভাবেই দেখি, কিন্তু এমন বৈশিষ্ট্য পড়ে সত্যিই আশ্চর্য লাগে যে উদ্ভিদও পরিবেশ থেকে শিখতে পারে)।
কাণ্ড ও শিকড়ের গঠন ও কার্যকারিতা
লজ্জাবতীর কাণ্ড বা স্টেম লতানে প্রকৃতির – পাতলা, সবুজ বর্ণের ও তুলনামূলক নরম ধরনের। যেহেতু গাছটি বড় হয় না, কাণ্ডটি শক্ত কাঠবাদাম কিংবা কাণ্ডলতা নয়, বরং ঘাসফুলের মতো একটু শক্ত, তন্তুযুক্ত কাঠামো। কাণ্ডের ভেতরে অন্যান্য সপুষ্পক উদ্ভিদের মতই জাইলেম (xylem) ও ফ্লোএম (phloem) টিস্যু রয়েছে। এই জাইলেম দ্বারা মাটি থেকে শিকড়ের মাধ্যমে জল ও খনিজ লবণ ওপরে পাতার দিকে উঠে যায়, আর ফ্লোএম দিয়ে পাতায় সংশ্লেষিত খাবার (শর্করা) নিচে গাছের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয় – একে সহজে বলতে গেলে উদ্ভিদের জলবাহী নল ও খাদ্যবাহী নল। কাণ্ডের ছেদন করলে রিং আকারে বেড় ধরে থাকা জাইলেম-ফ্লোএমের স্তর দেখা যেতে পারে (যদিও লজ্জাবতীর মতো সরু কাণ্ডে খালি চোখে আলাদা করে দেখা কঠিন)। কাণ্ডের বাইরে থাকে অ্যাপিডার্মিস ও কর্ক, যা তাকে রক্ষা করে, আর ভিতরে ক্যাম্বিয়ামের কারণে গাছ কিছুটা মোটা হতে পারে বয়স বাড়ার সাথে (তবে সরু লতানো গুল্ম হওয়ায় খুব বেশি দ্বিকাষ্ঠীয় বৃদ্ধির সুযোগ পায় না)।
শিকড়ের রহস্য: লজ্জাবতীর শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত মাটির নিচে ছড়িয়ে পড়তে পারে না, কারণ গাছটিই ছোট। সাধারণত এক থেকে দেড় ফুট গভীরতায় এদের মূলতন্ত্র সীমাবদ্ধ। taproot (মূলমূল) থেকে কিছু পার্শ্বমূল বের হয়। শিকড়ের গিঁটে (root nodules) একটা চমক আছে – অন্যান্য অনেক ফ্যাবাসিয়ি গাছের মতো লজ্জাবতীর শিকড়েও ছোট ছোট গাঁটের মতো গঠন দেখা যায়। এই নডিউল বা গাঁটগুলোতে Rhizobium গণের ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে যেটা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন ধরে উদ্ভিদকে সরবরাহ করে। অর্থাৎ লজ্জাবতী নিজের সার নিজেই বানাতে পারে এক অর্থে, যেহেতু নাইট্রোজেন স্থিরীকরণের মাধ্যমে মাটিকে উর্বর করছেyoutube.com। গ্রামের মানুষ দেখেছেন, যেখানে লজ্জাবতী জন্মায় সেই মাটিতে পরবর্তী অন্যান্য উদ্ভিদ ভালো জন্মায় – এর পেছনে রহস্য এই রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়ার অবদান। আমি যখন এটা প্রথম জানলাম, সত্যিই অবাক হয়েছিলাম। ভাবুন, একটা ছোট আগাছা টাইপের গাছ আশেপাশের মাটিকেও উর্বর করে দিচ্ছে বন্ধু-ব্যাকটেরিয়াদের কল্যাণে!
শিকড়ের আরেকটা দিক হল এগুলো মাটির উপরের দিকে কিছুটা প্রসারিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, তাই হেঁটে যেতে গিয়ে হঠাৎ এই লতার ঝাপটা পায়ে জড়িয়ে গেলে গাছ সহজে উপড়ে আসে না। অনেকেই বলবেন "আগাছা" গাছের খুব বেশি – মাটিতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে, সহজে মারা যায় না। এর পিছনে শিকড়ের এই ব্যাপক ছড়িয়ে থাকা নকশা কাজ করে।
স্পর্শে পাতার নড়নে সংশ্লিষ্ট কোষ ও জৈবরস
পাতার সিসমোন্যাস্টিক চলন নিয়ে আগেই বলেছি যে কোষের টার্গর চাপ কমে যাওয়াই মূল কারণ। এখন আরও একটু ভেতরের কাহিনী শোনাই – পালভিনাস (pulvinus) নামক অঙ্গটি এই নড়াচড়ার নায়ক। এটি পাতার গোড়ার ফোলা অংশ, সেখানে বিশেষ ধরনের পাতলা প্রাচীরের প্যারেঙ্কাইমা কোষ থাকে, যা জল ধরে রাখতে পারে ও দ্রুত জল ছেড়েও দিতে পারে। এই পালভিনাসে দুটি দিক থাকে: উপরের দিকের কোষ ও নিচের দিকের কোষ। স্বাভাবিক অবস্থায় উপর-নিচ দু’দিকের কোষেই পর্যাপ্ত পানি ভরা থাকে ও উভয় দিকে সমান টান (turgor) থাকায় পাতা খুলে প্রসারিত থাকে। স্পর্শ উদ্দীপনার পর নিচের পাশের কোষগুলো হঠাৎ তাদের পানি ছেড়ে দেয় (আয়ন, বিশেষত পটাশিয়াম বের হয়ে যায়, ফলে ওসমোসিসে পানি বের হয়)jagonews24.com, তখন উপরিভাগের কোষের টান পাতা টেনে ভাঁজ করে ফেলে। এজন্যই পাতাটি নিচের দিকে মুড়িয়ে যায়, যেন পাতার নিচ পিঠটি উপরের পিঠের সাথে লেগে যায়। এই পুরো খেলায় কোন জৈবরসের ভূমিকা? আসলে অ্যাসিটাইলকোলিনসহ কিছু রাসায়নিক সংকেতও উদ্দীপনার সময় নিঃসৃত হয় বলে জানা গেছে, যা স্নায়বিক নয় কিন্তু কোষগুলোর ব্যবহারে পরিবর্তন আনেshoshobdo.com। আমি ভাবতাম শুধুই পানি বেরিয়ে যাওয়াই কাজ, কিন্তু দেখা যাচ্ছে উদ্ভিদ হরমোন ও রাসায়নিকও বিষয়টাকে মডুলেট করে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু বিশেষ রাসায়নিক দিলে (যেমন লবণের দ্রবণ) পাতার সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় বা বেশি সময় লাগে – বুঝাই যায়, জৈবরসের ভারসাম্য নড়াচড়ার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।
এতক্ষণ যে ছবিটা পেলাম তা হচ্ছে: উদ্ভিদের কোষ, আয়ন, পানি, রাসায়নিক সঙ্কেত – সব মিলে এক অদ্ভুত সমন্বয়, যার ফলাফল স্পষ্ট চোখে দেখা যায় পাতার নড়াচড়ায়। আর এই জন্যই লজ্জাবতীর মত উদ্ভিদকে নিয়ে শুধু আমরা মজা করিই না, বিজ্ঞানীরাও অনেক গবেষণা করেন।
কাঁটা গঠন ও কাণ্ডের কোষবিন্যাস
কথা হচ্ছিল গাছের কাণ্ডের, সেখানে থাকা ছোট ছোট কাঁটাগুলো আসলে কীভাবে গঠিত হয়? উদ্ভিদের দেহে অনেক সময়ই কাঁটা গঠন হল পরিবর্তিত অঙ্গ (modified organ)। যেমন ক্যাকটাসে কাঁটা হল পাতার পরিবর্তিত রূপ, গোলাপের কাঁটা হল এপিডার্মিসের উৎপত্তি। লজ্জাবতীর ক্ষেত্রে কাঁটা মূলত কাণ্ডের বাহ্যিক ত্বকের কিছু কোষের রূপান্তর, বিশেষ করে stipule অংশের রূপান্তরিত শক্ত অংশ হিসেবে বিবেচিত। কাণ্ডের কোন কোন অংশে যে কাঁটা বের হয়, সেখানে কোষবিন্যাস (cellular arrangement) একটু আলাদা – বাড়তে বাড়তে ওই বিশেষ জায়গার কোষগুলি কাঠিন্য অর্জন করে এবং বাড়া বন্ধ করে চোঙার মতো বের হয়ে থাকে, ফলে ধারালো কাঁটার সৃষ্টি হয়।
যে কারণে এদের অনুন্নত কোষবিন্যাস বলা হয় – অর্থাৎ স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্পন্ন হয় না, মাঝপথেই রূপান্তর ঘটে। বোটানির ভাষায়, এগুলোকে প্রিকল (prickle) বলা যায়, যেটা আসলে গোলাপের কাঁটার মতোই এক ধরনের কিউটিকলার কাঁটা। এর ফাংশন খুব স্পষ্ট – গাছটিকে তৃণভোজী প্রাণীর থেকে রক্ষা করা। ছোট গাছ বলে এটি বিশেষ অসহায়; তাই ছোট এই কাঁটাগুলোই এর সুরক্ষা প্রহরী। আমি এদেরকে উদ্ভিদের ছোট্ট "ডিফেন্স সিস্টেম" বলে ডাকি। এই কাঁটার কারণে হয়ত কোনো প্রাণী মুখ দিয়ে খেতে গেলে ব্যথা পাবে, গাছ বেঁচে যাবে।
পুষ্টি উপাদান ও রাসায়নিক গঠন
লজ্জাবতী গাছ অবশ্য আমাদের খাদ্য নয়, তাই পুষ্টিগুণ নিয়ে বেশি কথা নেই। তবে ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে এর মধ্যে নানা রাসায়নিক উপাদান আছে, যেগুলো ওষুধি গুণ দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে Leaves ও Stems এ Mimosine নামক একটি alkaloid রয়েছে, যেটি কিন্তু বেশ বিষাক্ত alkaloid (Leucenine-এর মতো)herbfinder.himalayawellness.in,sphinxsai.com। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে Mimosa উদ্ভিদে পাওয়া বলে এর নাম mimosine। এই যৌগটির অল্প উপস্থিতি নানা রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করলেও অতিরিক্ত মাত্রায় এটা ক্ষতিকর হতে পারে। এছাড়াও পাতার নির্যাসে অ্যাড্রেনালিনের মতো পদার্থ পাওয়া গেছে – হ্যাঁ, যা আপনার পরিচিত হরমোন Adrenaline-এর মতো কাজের একটি উপাদানresearchgate.net।
তাই লজ্জাবতীর রস সেবনে কিছু উত্তেজক বা উদ্দীপক প্রভাবও দেখা যেতে পারে (যদিও আমরা এভাবে খাই না)। বীজে প্রচুর Mucilage (আঠালো পদার্থ) থাকে, যাতে গ্যালাক্টোজ ও ম্যানোজ জাতীয় সুগার আছে। এই মিউসিলেজ বীজ ভিজলে পিচ্ছিল জেলির মত হয় – অনেকটা ইসবগুল ভেজালে যেমন হয় আরকি। শিকড়ে Tannins নামক রাসায়নিক থাকেmpbd.cu.ac.bd, যা আমাদের কষাটে স্বাদযুক্ত ট্যানিন (যেমন চায়ের পানিতে থাকে) – এই ট্যানিন রোগ জীবাণু প্রতিরোধ এবং প্রদাহ হ্রাসে ভূমিকা রাখে। আরও আছে টর্গোরিন (turgorin) নামে এক ধরনের পদার্থ, যার নামকরণ টার্গর চাপের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে ধারণা করি। তাছাড়া সাধারণ উদ্ভিদের অন্যান্য উপাদান যেমন ফ্ল্যাভোনয়েড, স্টেরয়েড, গ্লাইকোসাইড ইত্যাদি পত্র, ফুল, মূলের নানা নির্যাসে পাওয়া যায়। এই বহুবিধ জৈবরাসায়নিক থাকার কারণেই লজ্জাবতী ঔষধি গুণে ভরপুর এক উদ্ভিদ হিসেবে খ্যাত। আবার সাবধানতার বিষয়ও আছে: গর্ভবতী মহিলা বা যাঁরা বিশেষ কিছু ওষুধ খান, তাদের ক্ষেত্রে লজ্জাবতীর উপাদান সমস্যা করতে পারে (এটা পরে বলছি)। মোটকথা, ছোট একটি উদ্ভিদের ভেতর রসায়নের ভাণ্ডার লুকানো আছে, যা মানবদেহে বিচিত্র প্রভাব ফেলতে সক্ষম।
ঐতিহ্যগত ঔষধি ব্যবহার
লজ্জাবতীকে অনেকে "ওষধের রাণী" বলে থাকেন এর বহুগুণের জন্যibnsinahealthcare.com। আমাদের লোকজ চিকিৎসায় এই উদ্ভিদ বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে। গ্রামের বড়দের কাছে জিজ্ঞাসা করলে শুনবেন: “লজ্জাবতী গাছ পিষে ক্ষতে লাগালে দ্রুত শুকায়”, “এর পাতার প্রলেপ ব্রণ সারাতে কাজে দেয়” – এমন অনেক টোটকা আছে। চলুন দেখি কোন কোন ক্ষেত্রে একে ব্যবহার করা হয়ঃ
-
ত্বকের সমস্যা: লজ্জাবতীর পাতা বেটে পেস্ট বানিয়ে ব্রণ (acne) ও মুখের কালো দাগের ওপর লাগালে উপকার হয় বলে প্রচলিত আছেjagonews24.com। এর অ্যান্টিসেপটিক বৈশিষ্ট্যে প্রদাহ কমে এবং ধীরে ধীদাগ হালকা হয়। কেউ কেউ মুখের ছোট ফোঁড়া বা অ্যালার্জি জনিত র্যাশেও এই পেস্ট ব্যবহার করে থাকেন।
-
ব্যথা ও বাত: গাছটির পাতা-শিকড়ে anti-inflammatory (প্রদাহনাশক) এবং analgesic উপাদান আছে বলে গাঁটের ব্যথা, স্নায়বিক ব্যথা বা বাতের ব্যথা উপশমে এর রস বা পেস্ট ব্যবহার করা হয়বিশেষ ককরা হয় লোকজ টোটকায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে এক বৃদ্ধ লোককে চিনি যিনি বাতের ব্যথায় লজ্জাবতীর শিকড় পানিতে সেদ্ধ করে সেই পানি খেতেন – তিনি বলতেন এতে তার ব্যথা কমে।
-
ক্ষত সারানো: যেকোনো কাটাছেঁড়া বা ঘা-খতের উপর লজ্জাবতীর পাতা বেটে লাগালে দ্রুত শুকিয়ে যায়। এর পেস্টে থাকা ট্যানিন এবং অন্যান্য পদার্থ ক্ষতের জীবাণু মারতেও সাহায্য করে এবং টিস্যু রিজেনারেশনে সহায়তা করে। অনেকেই ছোটখাটো রক্তপাত হলে পাতা চটকে রস বের করে ক্ষতে লাগিয়ে দেন গ্রামে।
-
ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: লজ্জাবতীর পাতা বা বীজের নির্যাস রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কিছুটা কমাতে সহায়ক বলে উল্লেখ আছে। প্রাচীন আয়ুর্বেদিক ব্যবহারেও এটা আসে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কখনও এসব ব্যবহারে এগোনো উচিত না – বিশেষ করে ডায়াবেটিসের মতো রোগে।
-
কফ-কাশি ও শ্বাসসমস্যা: পাতার বা ফুলের রস কাশি প্রশমনে ভালো কাজ করে বলে বলা হয়। এছাড়া হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টে কিছু ভেষজ মিশ্রণে লজ্জাবতী অন্তর্ভুক্ত থাকতো।
-
মূত্রকষ্ট ও পাথর: এই উদ্ভিদ মূত্রবর্ধক (diuretic) গুণের অধিকারী ,ফলে প্রস্রাব বাধাজনিত সমস্যায় এর মূলের রস খাওয়ানো হত আগে। মূত্রনালীর পাথর (vesical calculi) সরাতেও ব্যবহৃত হতো প্রাচীন চিকিৎসায়mpbd.cu.ac.bd। কেমন অবাক লাগে ভাবতে, ছোট একটা লতা এমন কাজে লাগতো!
-
নাড়িভুঁড়ির সমস্যা: আমাশয় (dysentery) বা পাতলা পায়খানায় লজ্জাবতীর মূলের প্রয়োগ ছিলো প্রচলিত। এটির কষাফল (astringent) ধর্ম পাচনতন্ত্রকে সংকুচিত করে এবং অতিরিক্ত বহিষ্করণ কমায়। এছাড়া পেটের গ্যাস-অম্বলেও পাতার রস কেউ কেউ খেতেনdailyjanakantha.com।
-
অন্যান্য: দাঁতের মাড়ি ফোলা বা ক্ষত হলে লজ্জাবতীর পাতা চিবানো বা রস লাগানো হতো (সোর গামস এর জন্য) । শিশুদের খিচুনি (convulsion) হলে নাকি লজ্জাবতীর রস পান করালে উপকার হয় – এমনও উল্লেখ আছে, যদিও আধুনিক ডাক্তাররা এভাবে ব্যবহার অনুমোদন করেন না। প্রাচীনকালে কুষ্ঠরোগ, জন্ডিস ইত্যাদিতেও এর ব্যবহার ছিল বলে বইপত্রে আছেmpbd.cu.ac.bd।
এই এতসব গুণের কারণে, লোকমুখে লজ্জাবতী "যাদুর গাছ" নামে বিখ্যাত। তবে খেয়াল রাখবেন – ঘরোয়া আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া খুব জরুরি। কারণ এর কিছু উপাদান অন্য ওষুধের সাথে বিক্রিয়া করতে পারে। বিশেষ করে গর্ভবতী বা স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য এটা নিরাপদ নাও হতে পারে। কাজেই ভেষজ হলেও, সচেতনভাবে ব্যবহারে মঙ্গল।
বৃদ্ধি ও পরিবেশগত চাহিদা
লজ্জাবতী গাছ প্রকৃতিতে আপনা আপনি জন্মায় বলেই আমরা জানি। বিশেষ যত্ন ছাড়াই যেখানে-সেখানে গজিয়ে ওঠে। তবু এর ভাল বৃদ্ধির জন্য কিছু পরিবেশগত শর্ত আছে। অভিজ্ঞতা থেকে আর বিভিন্ন উৎস থেকে যেটুকু বুঝেছি, তা হলো:
-
সূর্যালোক: পর্যাপ্ত রোদ্দুর পছন্দ করে লজ্জাবতী। খোলা স্থানে যেখানে দিনভর আলো পড়ে সেখানেই একে বেশি দেখা যায়। পুরো ছায়ায় এরা দুর্বল হয়ে যায়, পাতাও ঠিকমতো খোলে না। তবে আধাছায়া সহ্য করতে পারে। গাছটি যদি ঘরে টবেও লাগান, জানালার কাছে রৌদ্রোজ্জ্বল জায়গাতেই রাখুন।
-
তাপমাত্রা ও জলবায়ু: উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া এদের পছন্দ। ২০°-৩০°C তাপমাত্রা এর জন্য উপযুক্ত। খুব ঠাণ্ডায় (নিম্নতাপমাত্রা, বিশেষত ৫°С এর নিচে) গাছ টিকতে পারে না – পাতা ঝরে যায় ও মারা যায়। তাই শীতে এদের টিকে থাকতে কষ্ট হয়, যদিও শীতমণ্ডলীয় দেশে অনেকে গ্রীনহাউসে এদের বার্ষিক গাছ হিসেবে চাষ করেন।
-
মাটি: লজ্জাবতী অনুর্বর মাটিতেও জন্মাতে সক্ষম, কারণ আগেই বলেছি শিকড়ের ব্যাকটেরিয়া নাইট্রোজেন জোগায়। তবু দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ মাটি যেখানে পানি নিষ্কাশন ভালো, এমন মাটিতে দ্রুত বাড়ে। জলাবদ্ধ মাটি অপছন্দ এদের – অনেকদিন পানি জমে থাকলে শিকড় পচে যেতে পারে। মাটির pH খুব একটা বাধা নয়, অম্লীয় থেকে সামান্য ক্ষারীয় যে কোনও মাটিতে মানিয়ে নেয়।
-
পানি: মাঝারি সেচ দরকার। খুব বেশি পানি দিলে গাছ হলদে হয়ে যেতে পারে, আবার সম্পূর্ণ শুকনো খরাতেও টিকে থাকতে কষ্ট হয়। বৃষ্টি হোক আর না হোক, শিকড়ের গভীরে পানি খুঁজে নিতে পারে এরা, তাই টিকে যায়। তবে ইচ্ছাকৃত চাষ করলে নিয়মিত মাটি ভেজা রাখা ভালো, বিশেষ করে টবের গাছ হলে।
-
সার: যদিও আলাদা করে সার না দিলেও চলে, কিন্তু মাঝে মধ্যে জৈব সার দিলে গাছ আরও প্রচুর পাতা-ফুল দেয়। রাসায়নিক সারে বিশেষ দরকার হয় না, কারণ নিজেই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করছে। ফুল-ফল ধরার সময় অল্প ফসফরাস/পটাশ সারের জোগান দিলে বীজ বেশি হবে।
এককথায়, লজ্জাবতী টিকে থাকার জন্য খুব কঠিন দাবিদার নয়। বরং যেখানে প্রতিযোগিতা কম, একটু রোদ আছে, এমন জায়গায় এরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খেয়াল করবেন, পুকুর পাড় বা রাস্তার ধারে ঘাস থাকে না যেসব ফাঁকা জায়গায়, সেগুলো দখল করে লজ্জাবতী গালিচার মত বিছিয়ে যায়। প্রকৃতিতে নিজেদের জায়গা বানাতে এরা বেশ পারদর্শী! 💪
বীজ থেকে চারা তোলার পদ্ধতি
অনেকে শখ করে টবে বা বাগানে লজ্জাবতী লাগাতে চান – সত্যি বলতে এর মজাটা লাইভ দেখতে চাইলে নিজেই চাষ করতে পারেন সহজেই। বীজ থেকে চারা তোলার ঝামেলা কম, শুধু কিছু কৌশল জানা দরকার। আমি নিজে একটা সময়ে বীজ থেকে চারা করেছিলাম, সেই অভিজ্ঞতা আর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মিলিয়ে পদ্ধতিটা বলছি:
- বীজ সংগ্রহ: পূর্ণবয়স্ক লজ্জাবতী গাছে শুকনো বাদামী রঙের শুঁটি ফল থাকে। ওই শুঁটি হাতের আঙুলে চেপে ভাঙলে ভেতর থেকে ৩-৪টা ছোট কালো/বাদামি কঠিন বীজ পাওয়া যায়। এগুলোই সংগ্রহ করুন। যদি নিজে গাছ না পান, অনলাইনে Sensitive plant seeds নামে কিনতেও পাওয়া যায়।
- বীজ প্রস্তুত করা: লজ্জাবতীর বীজের খোলা বেশ শক্ত (হার্ড কোট)। সরাসরি মাটিতে দিলে অঙ্কুরোদ্গমে অনেক সময় লাগতে পারে বা কম গজাতে পারে। তাই Scarification বলে যে প্রক্রিয়া, তা করা ভালো। ঘাবড়াবেন না – সহজভাবে, শক্ত খোলটা নরম করা। আমি বীজগুলো এক রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর দিন লাগিয়েছিলাম। আপনি চাইলে গরম পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে নিতে পারেন (উত্তপ্ত পানিতে নয়, হালকা গরম)। এতে খোলটা ফুলে যাবে। কেউ কেউ স্যান্ডপেপার দিয়ে বীজের গায়ে হালকা ঘষে নেন যাতে খোল একটু পাতলা হয়। মোট কথা, বীজের ভিতরের ভ্রূণাংশ যাতে সহজে জল শোষণ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা।
- বপন: বীজ বোনার সময় ১/৮ ইঞ্চি গভীরে, খুব অল্প মাটি চাপা দিয়ে দিতে হয়sowrightseeds.com। দোঁআশ মাটির সাথে সামান্য জৈব সার মিশিয়ে নিতে পারেন মাটি প্রস্তুত করার সময়। একসাথে কাছাকাছি অনেকগুলো বীজ না বপন করাই ভালো – প্রতিটি চারা একটু জায়গা পেলে ভালো বাড়ে। টবে করলে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের প্রতি টবে ২-৩টা বীজ দিন, মাঠে করলে সারি করে ১ ফুট দূরত্বে দিন।
- জমি/টবের যত্ন: মাটিটা সব সময় ভেজা রাখুন কিন্তু পানিতে টইটম্বুর করবেন না (বীজ পচে যেতে পারে)। উষ্ণতাপমাত্রা দিলে (প্রায় ২৫°-৩০°C হল আদর্শ) বীজ দ্রুত অঙ্কুরিত হবে। ২১-২৮ দিনের মধ্যে চারা বের হয়ে আসার কথা, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতায় ১০-১৫ দিনেই ছোট টনটনে চারা মাথা তুলেছিল (সম্ভবত আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম বলে দ্রুত হয়েছে)। চারাগুলো যখন ২-৩ ইঞ্চি লম্বা হবে, তখন যদি খুব ঘন হয়ে যায় তবে আলাদা টবে প্রতিস্থাপন করতে পারেন।
- পরবর্তী পরিচর্যা: চারা অবস্থায় খুব বেশি পানি বা সার দরকার নেই, শুধু রোদ যেন পায় খেয়াল করবেন। ২-৩ মাসের মধ্যেই গাছ بالغ হয়ে যাবে, তখন ফুলও আসতে শুরু করবে। আমি দেখেছি যে বীজ থেকে বড় হওয়া লজ্জাবতী ৪-৫ মাস পরই বীজ দিতে শুরু করে – সাইকেলটি দ্রুত সম্পূর্ণ হয়।
চারা তোলার সময় একটা ব্যাপার খেয়াল রাখা জরুরি – দমকা হাওয়া বা অতিরিক্ত রোদে সদ্য অঙ্কুরিত চারাগুলো যেন শুকিয়ে না যায়। কারণ ছোট চারা খুব নাজুক, বাতাসে আর্দ্রতা কমে গেলে মরে যেতে পারে। তাই আপনি যদি গরমের মধ্যে চারা করেন, একটু ছায়া দিয়ে রাখুন শুরুতে বা সকালে-বিকালে পানি স্প্রে করুন। আর একটা মজার কথা, চারা অবস্থাতেই কিন্তু এর পাতা স্পর্শকাতর থাকে! আমি টুকটুকি চারাগুলোকেও আঙুল ছোঁয়ালে দেখি কুঁকড়ে যাচ্ছে – সত্যি মজার ছিল।
কাণ্ড-শিকড়ে ক্ষত হলে পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া
প্রকৃতিতে আগাছা গাছ টিকে থাকার নানা কৌশল আয়ত্ত করে। লজ্জাবতীর ক্ষেত্রে যদি কাণ্ড-শিকড় সংযোগস্থলে (ground level-এর কাছে) কোন কারণে ক্ষত হয় বা ভেঙে যায়, গাছটি ছোট বলে অনেকসময় মারা যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধারও হতে পারে। উদাহরণসরূপ, আমি দেখেছি একটা লজ্জাবতীর মূল অংশটা অর্ধেক উপড়ে গেছে গরু লেগে, তাও পরের সপ্তাহে দেখি পাশের গাঁট (node) থেকে নতুন ডাল বেরিয়েছে। এ ধরনের ঘটনায় ক্যালাস (callus) টিস্যু তৈরি হয়ে ক্ষতস্থানে ঝটপট কোষ বিভাজন শুরু হয়, যাতে আবার পরিবহন তন্ত্র জোড়া লাগানো যায়। এই প্রক্রিয়াটা অনেকটা যেমন আমাদের শরীরে ক্ষতস্থানে দাগ পড়ে মেরামত হয়, গাছেও সেরকমই। বিশেষত কাণ্ড যদি ভেঙে যায় আর শিকড় মাটিতে থাকে, শিকড় নতুন কুঁড়ি ফুটিয়ে তুলতে পারে। আরেকটা জিনিস, লজ্জাবতীর গাঁট থেকে সহজেই শিকড় বের হয় (many nodes are adventitious root capable)। তো, উপরের অংশ মরে গেলেও কোন একটা গাঁট মাটির সংস্পর্শে এলে আবার শিকড় বের করে নতুন করে বেঁচে উঠতে পারে। একে আমার কাছে অনেকটা "অংশ থেকে পুনর্জন্ম" মনে হয়। অবশ্য সবক্ষেত্রে তা হয় না – গাছটা পুরো শুকিয়ে গেলে আর কিছু করার নেই, কিন্তু দ্রুত বাড়ার কারণে নতুন বীজ থেকেও জায়গাটা পূরণ হয়ে যায়। তাই হয়তো আমরা খেয়ালও করি না কোনটা পুরনো গাছ ছিল, কোনটা নতুন গজালো – সবুজ গালিচা ঠিকই রয়ে যায়।
কাঠামোগত বিশ্লেষণ ও পরিমাপের কিছু কথা
বিজ্ঞানের আলোচনায় যদি একটু ঢুকে পড়ি, লজ্জাবতীর মতো উদ্ভিদ নিয়ে নানা ধরণের পরিমাপ করা যায়। উপরে পাতার নড়াচড়া নিয়ে ছোট্ট পরীক্ষা তো বললাম। এবার চিন্তা করি কাণ্ডের ভরবণ্টন বা জলপরিবহনের পরিমাপ নিয়ে। কোনো গাছের কাণ্ডে কতখানি জল চলাচল করে, বা কাণ্ডের ওজন কীভাবে বিভাজিত – এসব মাপার বিশেষ যন্ত্রপাতি লাগে। যদিও ঘরোয়া পর্যায়ে না পারলেও, কৌতূহল মেটাতে ধারণা দিতে পারি।
-
কাণ্ডের ভরবন্টন নির্ণয়: একটি পূর্ণবয়স্ক লজ্জাবতী গাছের বিভিন্ন অংশ (পাতা, কাণ্ড, শিকড়) শুকিয়ে ওজন করলে বুঝতে পারবেন কোন অংশে কেমন ভর। এই গাছটি মূলত পাতায় ভরা, ফলে total biomass-এর বড় অংশই পাতা ও শাখায় থাকে, শিকড়ে কম। ভরবন্টন বলতে যদি বোঝায় কাণ্ডের ভর সুষম কিনা – তাহলে বলবো, লজ্জাবতীর কাণ্ড পাতলা হলেও লতিয়ে থাকে বলে ওর ওপর খুব চাপ পড়ে না, মাটি ধরে রাখে। একে পরিমাপ করতে চাইলে আপনি কাণ্ডের দৈর্ঘ্য বরাবর বিভিন্ন অংশ কেটে আলাদা শুকিয়ে ওজন করতে পারেন। আমি করিনি, তবে ধারণা করি নিচের দিকে মোটা অংশ কিছু ভারী আর শীর্ষের দিকটা একদম হালকা ও পাতাসমৃদ্ধ।
-
জলবাহী টিস্যু পরিমাপ পদ্ধতি: কোনো উদ্ভিদের জাইলেম টিস্যু কতটা কার্যকরী, তা মাপা যায় বিভিন্ন উপায়ে। ধরা যাক আমরা জানতে চাই লজ্জাবতীর কাণ্ড দিয়ে জল চলাচলের হার কত। এক উপায় হল পটোমিটার (potometer) ব্যবহার করাsowrightseeds.com।
- এটি এক ধরনের যন্ত্র যেখানে গাছের ডালকে পানিভর্তি টিউবে সংযুক্ত করে পানি কমার হার দেখা হয়, যা আসলে গাছের ট্রান্সপিরেশন রেট (পরিবহন হার) নির্দেশ করে। আমি যদি লজ্জাবতীর একটি ডাল কাটতাম আর সেটা পানিভরা টিউবের মুখে আটকাতাম, দেখতাম সূর্যের তাপে কী গতিতে জল টানছে। হয়তো প্রতি মিনিটে কয়েক ফোঁটা করে নামবে। এরপর সেই হার দিয়ে হিসাব করা যায় ঘণ্টায় কত মিলিলিটার পানি গাছ টেনে নিচ্ছে – এটাই জাইলেম প্রবাহের পরিমাপ।
আরেকটু কারিগরি পথে গেলে, রঙ্গক (dye) প্রবাহ পরীক্ষা করতে পারি। রঙ মেশানো পানি (ধরুন লাল ফুড কালার) গাছের গোড়ায় দিলে কিছুক্ষণ পর কাণ্ড চিরে দেখবো লাল রঙ উপরে উঠে এসেছে কিনা। লজ্জাবতীর স্বচ্ছ সবুজ কাণ্ড, ধারণা করি এর ভাসকুলার বান্ডিলে সেই রঙ দেখা যাবে। কতদূর উঠেছে সেটা মেপে সময় দিয়ে ভাগ করলে জলউত্থানের গতি পাওয়া যাবে।
-
জাইলেম ও ফ্লোএম আলাদা মাপার কৌশল: এটা বেশ গবেষণামূলক ব্যাপার। জাইলেমের প্রবাহ আলাদা মাপা যায় কারণ সেটা মূলত পানি ও খনিজ টেনে নেয়, আপনি Dye ব্যবহার করে বা ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি দিয়ে দেখতে পারেন। কিন্তু ফ্লোএম (যা আহার রস বহন করে) মাপা কঠিন, কারণ তা খুব ধীরগতির এবং চাপের তারতম্যে নির্ভরশীল। বিজ্ঞানীরা কী করেন – একটি উপায় হল এফিড (aphid) পোকা দিয়ে ফ্লোএম রস সংগ্রহ করা। এফিড পোকা long stylet ঢুকিয়ে ফ্লোএম থেকে রস শোষণ করে; আপনি পোকাটি সরিয়ে স্টাইलेट রেখে দিলে নিজে নিজেই মধুরস বের হতে থাকবে (অসাধারণ কৌশল, তাই না?)। সেই রস কী গতিতে বেরোচ্ছে, কী পরিমাণ বেরোচ্ছে তা মাপা যায়। অবশ্য লজ্জাবতীর মত সরু গাছে এটা করা কঠিন, তবে বৃহত্তর গাছে এসব করা হয়। আর রাসায়নিক দিক দিয়ে বলতে গেলে, রেডিওআইসোটোপ ট্রেসার ব্যবহার করা একটা পদ্ধতি – যেমন কার্বন-১৪ সমৃদ্ধ CO₂ দিলে সেটা পাতায় খাদ্যে রূপান্তরিত হয়ে ফ্লোএম দিয়ে নেমে আসে, আমরা গাছে Geiger counter দিয়ে ট্র্যাক করতে পারি রেডিওঅ্যাক্টিভ চিনির গতি। একটু ভারী ব্যাপার হয়ে গেল। সহজ করে বলি – জাইলেমে রঙ্গক মিশিয়ে আর ফ্লোএমে চিনিতে চিহ্ন লাগিয়ে আমরা আলাদা ট্র্যাক করতে পারি কোনটা কতদূর যাচ্ছে। এইভাবে আমরা জানতে পারি জাইলেম দ্রুত প্রবাহিত হয়, ফ্লোএম তুলনামূলক ধীর (প্রতি ঘণ্টায় কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র হয়ত)।
-
ফল বিশ্লেষণের সূত্র ও চার্ট: পরিমাপ যদি করেই ফেলি, তবে তার ডাটা বিশ্লেষণও করতে হবে। আমি কল্পনা করছি, যদি পাতার ভাঁজ হওয়ার সময় বা জলের প্রবাহ নিয়ে পরীক্ষা করি, নিশ্চয়ই গ্রাফ আঁকব। উদাহরণসরূপ, সময়ের বিরুদ্ধে পাতার কোণ পরিবর্তনের গ্রাফ, বা বিভিন্ন তাপমাত্রায় ট্রান্সপিরেশন রেটের কলাম চার্ট। এগুলো করতে স্কুলের গাণিতিক জ্ঞানই যথেষ্ট – দ্রবণ সংক্রান্ত হিসাব, গড় বের করা, হার বের করার জন্য Δy/Δx নেয়া, ইত্যাদি। ধরুন, পটোমিটার দিয়ে দেখি দুপুরে ১ ঘণ্টায় ৫ mL পানি খরচ হল, সন্ধ্যায় ১ mL। তো একটা চার্টে সময় বনাম মিলিলিটার এঁকে দুইটা দাগ দিয়ে দিলেই বুঝা যাবে কখন বেশি ট্রান্সপিরেশন। অথবা পাতার নড়ার উদাহরণে, প্রথম স্পর্শে ২ সেকেন্ডে বন্ধ, দশম স্পর্শে ৫ সেকেন্ডে বন্ধ – এভাবে টাইম বনাম রেসপন্স টাইমের গ্রাফ আঁকলে একটি বাড়ন্ত রেখা পাবো, দেখে বলবো “গাছের সেন্সিটিভিটি কমছে”। আমার কাছে এই বিশ্লেষণের অংশটাও খুব ইন্টারেস্টিং লাগে – প্রকৃতির ঘটনার মধ্য থেকে তথ্য আর সংখ্যা বের করে আনা, এবং সেগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা পাওয়া। একেই তো বলে জ্ঞান অর্জন করা, তাই না?
সবশেষে, ভাবছেন এত কথা বলছি কেন? কারণ লজ্জাবতীর মত সাধারণ একটা উদ্ভিদ, যেটাকে আমরা শিশুকাল থেকে চিনি, তার ভেতরে লুকিয়ে আছে অসাধারণ সব বৈজ্ঞানিক কাহিনী। এটি আমাদের আনন্দ দেয়, কৌতূহল মেটায়, আবার প্রকৃতির জটিলতার এক সহজ উদাহরণ হিসেবেও দাঁড়িয়ে থাকে। আমি যখনই কোনো লজ্জাবতী গাছ দেখি, একটু ছুঁয়ে দেখি আর মুগ্ধ হয়ে যাই – লাজুক মেয়ের মত itself কে গুটিয়ে নেয়। তারপর মনে পড়ে, 'নিজে জানুন, অন্যকে জানান' – তাই আজকের আলোচনাটা আপনার সঙ্গে শেয়ার করলাম। আশা করি এই প্রবন্ধ থেকে লজ্জাবতী নিয়ে আপনার জানার ভাণ্ডার আরো পূর্ণ হয়েছে এবং পড়তে পড়তে মনে হয়েছে যেন কারো সাথে গল্প করেই সব জানলেন। এমন আরও নানা বিষয়ে জানতে মন চাইলে আমাদের সাথেই থাকুন। আমি তো শিখেই চলেছি, এবার আপনাকেও শিখিয়ে চললাম – এর মাঝেই সম্পূর্ণ তৃপ্তি!
একটা লাইন দিয়ে শেষ করি: প্রকৃতির প্রতিটি উপাদানই বিশেষ, যত জানতে যাবেন ততই চমকের শেষ নেই – ছোট্ট লজ্জাবতী তার জ্বলন্ত উদাহরণ।
শেষকথা
লজ্জাবতী গাছ আমাদের শিখিয়ে যায় যে প্রকৃতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সৃষ্টিতেও কত বড় আশ্চর্য লুকিয়ে থাকতে পারে। একটা ছোট্ট আগাছার মত উদ্ভিদ কিভাবে স্পর্শে সাড়া দেয়, বিজ্ঞান আমাদের বলেছে সেটি তার প্রতিরক্ষা কৌশল – কোষের ভেতরের টার্গর চাপ হঠাৎ কমে গিয়ে পাতা মুড়ে ফেলে, যেন শিকারীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়। দিনের শেষে আবার সে স্বাভাবিক হয়ে সূর্যের আলো গায়ে মেলে ধরে। এই সরল আচরণের মধ্যে লুকিয়ে আছে গভীর বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং প্রকৃতির নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা।
লজ্জাবতী শুধু মজার আচরণের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, এর আছে বেশ কিছু ঔষধি গুণাগুণও। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় দীর্ঘদিন ধরে লজ্জাবতী ব্যবহার হচ্ছে – এর পাতার রস ক্ষত সারাতে, যান্তব্যথা উপশমে বা অর্শ রোগে উপকারী বলে মনে করা হয়। আধুনিক গবেষণাও ইঙ্গিত দিচ্ছে যে এই গাছের নির্যাস রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, রক্তে শর্করা কমানো, প্রদাহ হ্রাস এবং মানসিক চাপ দূর করতে সহায়তা করতে পারে। ভাবতে অবাক লাগে, যেই গাছকে আমরা ছোটবেলায় শুধুই খেলাচ্ছলে স্পর্শ করে মজা পেতাম, সেই গাছই প্রাকৃতিক ঔষধের এক ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, যেকোনো ভেষজের মতো অতিরিক্ত ব্যবহার ঠিক নয় এবং বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থা) চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।প্রকৃতির এই “লাজুক” উপহার আমাদের শিখিয়েছে বিনয়ের সৌন্দর্য এবং জ্ঞানের বিনম্রতা। লজ্জাবতী গাছ হারিয়ে যেতে বসেছে বলে শোনা যায়, কিন্তু আমাদের সচেতনতা ও আগ্রহই পারে এই উদ্ভিদটিকে বাঁচিয়ে রাখতে। হয়তো নিজের বাগানে একটি লজ্জাবতী লাগানোর মাধ্যমে আমরা আমাদের শৈশবের বিস্ময়কে আবার কাছে টানতে পারি। এই ছোট্ট গাছটি মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান – যত সাধারণই হোক – বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লজ্জাবতীর লাজুক সাড়া যেন আমাদের বিনয়ী হতে ও প্রকৃতির সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে অনুপ্রাণিত করে। জীবনের পথে কখনো যদি ক্লান্ত লাগে, লজ্জাবতীর স্পর্শে পাতা বুজে যাওয়ার দৃশ্যটা মনে করুন; দেখবেন, অদ্ভুত এক প্রশান্তি ও কৌতূহল আপনাকে নতুন করে শক্তি দেবে।
Call to Action
লজ্জাবতী গাছ নিয়ে আপনার কোনো মজার অভিজ্ঞতা বা প্রশ্ন থাকলে নিচে মন্তব্য করে আমাকে জানান। এই লেখা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে, তবে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন – যাতে তারাও এই আশ্চর্য উদ্ভিদটির সম্পর্কে জানতে পারে। জ্ঞান ভাগাভাগির এই প্রয়াসে সামিল হোন এবং মনে রাখুন: “নিজে জানুন, অন্যকে জানান।”
প্রশ্নোত্তর (FAQ)
প্রশ্ন: কীভাবে লজ্জাবতী গাছ রোপণ ও পরিচর্যা করব?
উত্তর: লজ্জাবতী গাছ রোপণ করা বেশ সহজ এবং মজার। এটি উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভালো জন্মে, তাই পর্যাপ্ত রোদ পড়ে এমন জায়গায় গাছটি লাগান। দোআঁশ ও জলনিষ্কাশনযুক্ত মাটিতে লজ্জাবতী সবচেয়ে ভালো বাড়ে – পানি জমে থাকে এমন মাটি এড়িয়ে চলুন। চারা বা বীজ থেকে লাগানো যায়; বর্ষাকালে বীজ বুনলে সহজে অঙ্কুরোদগম হয়। গাছের মাটি সবসময় একটু ভেজা রাখবেন, তবে বেশি জলে ডুবিয়ে রাখবেন না (মাটির উপরের স্তর শুকালে তবেই পানি দিন)। লজ্জাবতী মূলত আগাছার মতো দ্রুত বাড়ে, তাই বেশি সার বা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। পাত্রে লাগালে উজ্জ্বল জানালার কাছে রাখুন। নিয়মিত আলতো করে ডাল ছাঁটলে গাছটি ঝোপালো ও সুন্দর থাকে। মনে রাখবেন, এটি খুব সূর্যালোক পছন্দ করে – যদি পর্যাপ্ত আলো না পায়, তবে পাতা দিব্যকালেও বন্ধই থেকে যায়।
প্রশ্ন: লজ্জাবতী গাছ স্পর্শ করলে পাতা বন্ধ হয়ে যায় কেন?
উত্তর: লজ্জাবতীর এই লাজুক আচরণের পেছনে চমৎকার বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। গাছটির পাতায় স্পর্শ করলে বা নাড়াচাড়া হলে তাতে বৈদ্যুতিক সংকেত প্রবাহিত হয়। ফলস্বরূপ, পাতার কোষগুলোর ভেতরে থাকা তরল (টার্গর চাপ) দ্রুত স্থানান্তরিত হয়ে যায়, এবং নিমেষেই পাতা বেকে যায় বা ঝিমিয়ে পড়ে। এটিকে সিসমোন্যাস্টিক চলন বলে – এক ধরনের প্রতিরক্ষা কৌশল যেখানে গাছটি নিজেকে অরুচিকর বা মৃত বলে ভান করে যেন তৃণভোজী প্রাণীরা এটিকে খাবার ভেবে কাছে না আসে। কয়েক মিনিট পর কোষগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলে পাতাগুলোও আবার প্রসারিত হয়ে যায়। এছাড়াও সন্ধ্যা হলে বা বেশি তাপমাত্রাতেও লজ্জাবতীর পাতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায় – এটিকে নিকটিন্যাস্টি বলে, যা গাছের জৈবঘড়ির অংশ।
প্রশ্ন: লজ্জাবতী গাছের ঔষধি গুণাগুণ কী কী?
উত্তর: লজ্জাবতী বহুদিন ধরে ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর পাতা, মূল ও ফুলে এমন কিছু প্রাকৃতিক যৌগ আছে যা নানা রোগ প্রতিরোধে সহায়ক। উদাহরণ হিসেবে, লজ্জাবতীর পাতার রস ক্ষতস্থানে দিলে দ্রুত ঘা শুকোতে সাহায্য করে এবং ব্রণ বা চর্মের দাগ হালকা করতেও ব্যবহৃত হয়। গাঁট ও কোমর ব্যথা, আর্থ্রাইটিসের ব্যথা উপশমে লজ্জাবতীর পাতা বা শিকড়ের পেস্ট কার্যকর বলে লোকজ বিশ্বাস। গবেষণায় আরও দেখা গেছে, এই উদ্ভিদের নির্যাস রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে এবং উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সহায়তা করে। লজ্জাবতীর কিছু উপাদান প্রদাহ-নাশক (অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি) ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণও প্রদর্শন করে, যা দেহের কোষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদে এটি অনিদ্রা ও উদ্বেগ কমাতে ব্যবহৃত হতো – পাতার হালকা চা স্নায়ুকে শিথিল করে মানসিক শান্তি দেয়। অবশ্য যে কোনো ভেষজের মতোই অতিমাত্রায় ব্যবহার না করাই ভালো এবং ব্যবহার শুরুর আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
প্রশ্ন: লজ্জাবতী গাছ কোথায় জন্মে এবং কী ধরনের পরিবেশ পছন্দ করে?
উত্তর: লজ্জাবতী মূলত ট্রপিক্যাল অঞ্চলের উদ্ভিদ, যার আদি নিবাস মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা বলে জানা যায়। এখন এটি বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জসহ বিশ্বের বহু উষ্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। উন্মুক্ত রোদ-পাওয়া ঘাসযুক্ত স্থান, পথের ধারে, জমির আইলে কিংবা জঙ্গলের প্রান্তে এই লতা আগাছার মতো আপনিই জন্মাতে পারে। বাংলাদেশে আগে মাঠেঘাটে প্রচুর দেখা মিলত লজ্জাবতীর, যদিও আজকাল আগের তুলনায় কম দেখা যায়। গাছটি আর্দ্র আবহাওয়া ও উষ্ণ তাপমাত্রা পছন্দ করে। বর্ষাকালে এর বংশবৃদ্ধি বেশি হয়, তবে উপযুক্ত পরিবেশ (ভাল রোদ ও মাটি) পেলে বছরের অন্য সময়ও জন্মাতে পারে। একটা মজার ব্যাপার হলো, লজ্জাবতীর বীজগুচ্ছগুলোতে ছোট ছোট কাঁটাযুক্ত বুর থাকে, যা জন্তু-পাখির গায়ে লেগে দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এজন্য অনুকূল পরিবেশে গাছটি খুব দ্রুত আশেপাশে ছড়িয়ে যায়। কিছু দেশে এটিকে আক্রমণাত্মক আগাছা বলে মনে করা হয়, কারণ এর বীজ খুব সহজে ছড়িয়ে গিয়ে পুরো এলাকাজুড়ে চারা গজাতে থাকে। তবে আমাদের দেশে এটি পরিচিত প্রাকৃতিক ভেষজ সম্পদ হিসেবেই বেশি সমাদৃত।
প্রশ্ন: লজ্জাবতী গাছকে বারবার ছুঁলে গাছের কোনো ক্ষতি হয় কি?
উত্তর: অনেকেই আমাদের শৈশবে মজা করে লজ্জাবতীর পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বন্ধ করিয়েছি। মাঝেমধ্যে এভাবে স্পর্শ করলে গাছের খুব ক্ষতি হয় না – কয়েক মিনিট পরই পাতা খুলে যায় এবং গাছ স্বাভাবিক কাজকর্ম (যেমন সংশ্লেষ) চালিয়ে যায়। তবে অতিরিক্ত বারবার ছোঁয়া গাছটির জন্য ভাল নয়। বারবার পাতাগুলো বন্ধ হলে গাছের শক্তিক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, একটানা আঘাত পেতে থাকলে গাছ কিছু সময় পরে প্রতিক্রিয়া দেখানো কমিয়ে দেয়, অর্থাৎ অভ্যাসগতভাবে স্পর্শকে উপেক্ষা করতে শেখে। এটি গাছের জন্য一স্ট্রেস বা চাপের লক্ষণ। তাই নেহাত কৌতূহলবশে মাঝে মাঝে ছুঁতে পারেন, কিন্তু খেলাচ্ছলে খুব ঘন ঘন লজ্জাবতীর পাতা বন্ধ করা ঠিক হবে না – এতে উদ্ভিদটি দুর্বল হয়ে যেতে পারেfacebook.com। আমাদের উচিত প্রকৃতির এই জীবন্ত খেলনাটির প্রতি বিবেচনা দেখানো এবং তাকে অতিরিক্ত বিরক্ত না করা। (একটুখানি ছুঁয়ে তার লাজুক প্রতিক্রিয়া দেখা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়!)
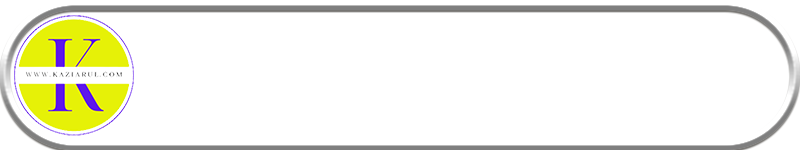








কাজীআরিফুল ডট কমে নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url